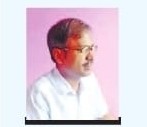গান্ধিজির স্বপ্নের ভারতের সঙ্গে একেবারেই বিপরীতমুখী এখনকার ‘নব ভারত নির্মাণ’ –
নজরুল ইসলাম (শিক্ষক)
” মহাত্মা গান্ধি যে ভবিষ্যৎ ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন সেখানে প্রতিটি ভারতীয় তার নিজ ধর্ম, ভাবউনা, পেশা ও সংস্কৃতিগত স্বতন্ত্রতা বজায় রেখেও বৃহত্তর ভারতীয় জাতির একজন সদস্য হবেন। কিন্তু বর্তমান ভারত তার ঠিক বিপরীত মুখে চলছে। আগামীকাল ৩০ জানুয়ারি গান্ধি হত্যা দিবসকে স্মরণে রেখে লিখেছেন নজরুল ইসলাম “
প্রতিবেদন :- উগ্র জাতীয়তাবাদ তথা হিন্দুত্ববাদের অভূতপূর্ব জাগরণে দেশের সব পথ এসে মিশে যাচ্ছে অযোধ্যার জনমানসে এমন দাবি অনেকটাই প্রতিষ্ঠিত। স্বভাবতই অযোধ্যা বিজয় হিন্দুত্ববাদীদের বৃহত্তম রাজনৈতিক সাফল্য হিসেবে চিহ্নিত হলেও দর্শনগত দিক দিয়ে মহাসাফল্য ছিল ১৯৪৮ সালের ৩০ শে জানুয়ারি জাতির জনক গান্ধী হত্যা। প্রকৃতপক্ষে এই হত্যাকান্ডের অন্তরালে ব্যক্তি হত্যা নয়, ছিল একটি আদর্শকে হত্যা করার অপচেষ্টা। অবশ্য ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, কোনও নির্দিষ্ট আদর্শের অনুসারী ব্যক্তিকে হত্যা করা গেলেও তাঁর আদর্শকে হত্যা করা যায় না। এ কথা বিলক্ষন সত্য যে, ইতিহাস প্রবাহমান। যেহেতু ইতিহাস বারবার ফিরে আসে, তাই তার কাছে থেকে একবার নয়, শিক্ষা নিতে হয় বারবার। ইতিহাসের স্রোতধারায় গান্ধী হত্যা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির নিকট প্রাথমিক সাফল্য, বাবরি মসজিদ ধ্বংশ ও রাম মন্দির নির্মাণ মহা সাফল্য হিসেবে বিবেচিত। এরূপ সাফল্য অর্জনকারী কুশীলবগণ অধুনা ভারতীয় সংবিধানের অনুপম সৌন্দর্যকে বিনষ্ট করার মহাযজ্ঞে শামিল হয়ে যুগান্তকারী সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে অবিচল। ইতিহাসের পুনঃনির্মাণের বৃহত্তর ময়দানে তাদের আস্ফালনের অসম প্রতিযোগিতার সামনে সুশীল নাগরিক সমাজের কাছে শহীদ দিবসের স্মরণে’ মহাত্মা’র মাহাত্ম্য অনুসন্ধান বিবেকের দাবি রাখে। গান্ধীর রাজনৈতিক দর্শনের সঙ্গে হিন্দু দক্ষিণপন্থার বিরোধ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সরল সমীকরণের পথ ধরে চলেনি। আপাত দৃষ্টিতে স্পষ্ট বিভাজন রেখা দৃশ্যমান না হলেও একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে অগ্রসর হয়েছে, যেখানে মধ্যপন্থী চেতনার প্রভাব ছিল সক্রিয়। গান্ধীও হিন্দু ভারতের অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। হিন্দুত্ববাদীরা হিন্দু ধারণার পাশাপাশি তাদের অদম্য ইচ্ছা শক্তিকে সংগঠিত করেছিল হিংস্রতার মাধ্যমে ভারত থেকে মুসলিমদের সম্পূর্ণ মুছে দেওয়া বা তাদের সর্বাংশে দমিয়ে রাখতে। আর গান্ধী চেয়েছিলেন ক্ষমতার আস্ফালন থেকে সরে এসে মুসলমানদের প্রতি উদার সহিষ্ণু ও সহাবস্থানের নীতি অনুসরণ করতে গান্ধীর দৃষ্টিতে অহিংসা হিন্দু ধর্মের কেন্দ্রীয় তথা মৌলিক তত্ত্ব। এটাই হিন্দু ধর্মের প্রাণ শক্তি। হিন্দু ধর্মের প্রকৃত অনুসারীদের অন্তরের সম্পদ এবং সনাতন ঐতিহ্য ও বটে। ক্ষমতা, হিংসা ও উগ্রতার কলঙ্ক দ্বারা হিন্দু ধর্মের এই সনাতন ঐতিহ্যকে তিনি বিসর্জন দিতে মোটেই রাজি ছিলেন না। এর বিপরীতে অবস্থানরত দক্ষিণপন্থী হিন্দুত্বের অনুসারীদের মোটেই তা পছন্দেরও বিষয় ছিল না।
গান্ধী অনুসৃত কালজয়ী ‘অহিংসা’ ও ‘সত্যাগ্রহ নীতির মূল কথাই ছিল সত্যের দ্বারা মিথ্যাকে জয়, অহিংসার দ্বারা হিংসাকে জয়, মনে প্রাণে হিংসাকে বির্ষজন, শত্রুর যারা শত অত্যাচারিত হয়েও প্রতিকার কল্পে কোন ধরনের প্রতিশোধ গ্রহণ না করেও শত্রুর বিবেক জাগরণের জন্য সত্যের পথে অবিচল থাকা। কঠোর বাস্তবতার নিরিখে সমালোচনা করেও এমনকি তাঁর বড় ধরনের নিন্দুকেরাও স্বীকার করে থাকেন যে, বিনা অস্ত্রে, বিনা রক্তপাতে, কোনও বীরত্ব প্রদর্শন না করেও কেবলমাত্র একটি কল্পিত বিশ্বাসের প্রতি আস্থা রেখে লক্ষ্যে অবিচল অবস্থান নিয়ে গান্ধীজি শত্রু-মিত্র উভয়ের মন জয় করেছিলেন। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ ভারতে সাজাজ্যবাদ বিরোধী জনমত গঠনে ও সাংগঠনিক প্রয়োজনে গান্ধী, ধর্মীয় পুনরুত্থানবাদের একটি রূপ-কে ব্যবহার করেছেন। এই মঞ্চে তিনি কেবলমাত্র হিন্দু ধর্মের অনুসারীদেরই নয়, অন্য ধর্মাবলম্বীদেরও শামিল করতে চেয়েছিলেন। উনিশ শতকের শেষার্ধে আর্থ সমাজের সংস্কারবাদী আন্দোলনে হিন্দু পুনরুত্থানবাদের প্রভাব ছিল সক্রিয়। গান্ধীর ওপর এর প্রভাব থাকলেও পার্থক্য ছিল সুস্পষ্ট। আর্য সমাজের’শুদ্ধি আন্দোলন’ এ ধর্মান্তরিতদের হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনার প্রয়াস সক্রিয় থাকলেও গান্ধী সে পথে হাঁটেননি। গান্ধী ভারতের জাতি কল্পনায় মুসলিমদের চিহ্নিত করেছিলেন’ভাই’ হিসেবে, দলিতদের দিতে চেয়েছিলেন সামাজিক মর্যাদা। হিন্দুদের সঙ্গে দলিতদের পার্থক্য তাঁর কাছে গ্রহণীয় ছিল না। হিন্দু ধর্মাশ্রিত সংস্কারবাদীদের গঠনমূলক চেতনা ও ধারার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব থাকা সত্ত্বেও গান্ধী নিজেকে ‘সনাতনী ‘হিন্দু হিসেবে পরিচয় দিতে পছন্দ করতেন। যা ছিল প্রচলিত হিন্দু সংস্কারবাদের মূলধারার বিপ্রতীক অবস্থান।
গান্ধীজী ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির পৃথকীকরণ করেননি, এটা যেমন সতা, তার চেয়ে অধিক সত্য যে, তিনি উগ্র ধর্মীয় চেতনা স্পষ্টভাবে বললে উগ্র হিন্দুত্ববাদী ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে রাজনীতির মিশ্রণ ঘটাননি। তিনি মনে করতেন ধর্মই নৈতিকতার একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য উৎস। তাই যে রাজনীতি ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়, গান্ধীজী স্পষ্টভাবে তাকে প্রত্যাখ্যান করে ছিলেন। পাশ্চাত্য অনুসৃত ধর্ম বিবর্জিত তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে তিনি সাদরে গ্রহণ করেননি, বরং এড়িয়ে চলেছিলেন। কারণ, তাতে গাল ভরা উচ্চ আদর্শের আধিক্য থাকলেও নৈতিকতার প্রাণশক্তি ছিল ক্ষীণ ‘হিন্দ-স্বরাজ’ এ ভোগ সর্বস্ব বৈষম্যমূলক পাশ্চাত্য সভ্যতাকে তিনি ব্যাধি হিসেবে চিহ্নিত করেন। প্রাচ্যের পক্ষে নিজের আত্মাকে বিসর্জন দিয়ে পাশ্চাত্যকে গ্রহণ করা সমীচীন নয়- এটাই ছিল তাঁর স্বতন্ত্র দর্শন। গান্ধীর আত্মজীবনী দ্য স্টোরি অব মাই এক্সপেরিমেন্ট উইথ টুথ’ (১৯২৫-২৯) এর ছত্রে ছত্রে এর প্রতিফলন ঘটেছে।
প্রাচ্যের আত্মার সন্ধান অন্বেষণ করেছেন গান্ধীজী ভারতবর্ষের চিরাচরিত বহুত্ববাদী চেতনা, সম্প্রীতি, সহাবস্থান, মূল্যবোধ আর সহনশীলতার মাঝে। ভারতের জাতীয় আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসেবে জনমানসে গান্ধীজী তাই কার্যত সর্বজনীনভাবে সমাদৃত। আড়ালে তাঁর সমালোচনাকারীরাও প্রকাশ্যে তাঁর সমর্থক হন। এই পথেই গান্ধীজি আমাদের দেশের ইতিহাসে নয়, জাতীয় জীবনেও তিনি ‘মিথ’-এ পরিণত হয়েছেন। অবশ্য ভোট সর্বস্থ রাজনীতির খোলা ময়দানে সংখ্যাগরিষ্ঠের আবেগ জাগরণের লক্ষ্যে ‘ঈমান’ (বিশ্বাস)ও ‘আমল’ (পালনীয়)-উভয়ের মধ্যে পার্থক্য। বিস্তর। স্বাধীনতা সংগ্রামের অস্থিরতার দিনগুলিতে গান্ধীজীর ছিল এক স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি। একথা বলা হয়ে থাকে যে, সার্বিক গণআন্দোলনে ছিল গান্ধীজীর চূড়ান্ত ভীতি। এই মত অতি সরলীকরণ দোষে দুষ্ট। প্রকৃতপক্ষে গণআন্দোলন সম্বন্ধে গান্ধীজীর মূলনীতি হিল এই রকম, সাধারণ মানুষের সম্মিলিত প্রতিরোধ তথা গণসংগ্রামকে তিনি স্বচালিত হতে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। যারা ধর্মীয় ভাবাবেগ নয়, আধ্যাত্মিকভাবে এবং নৈতিকভাবে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিতে যোগ্যতর, আন্দোলনের ভার তাদের ওপর রাখার পক্ষপাতি ছিলেন। শক্তিশালী ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রীয় শক্তির সাথে শক্তিহীন উপনিবেশিক প্রজার লড়াইয়ে তিনি শিক্ষিত সচেতন মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে স্বার্থত্যাগী ও নৈতিক বলে বলীয়ান করে তুলতে চেয়েছিলেন। কথিত আছে, গান্ধীজীর অহিংস নীতির একনিষ্ঠ অনুসারী খান আব্দুল গফ্ফার খান ইতিহাসে যিনি সীমান্ত গান্ধী’ নামে পরিচিত, তাঁর বার বার কারাবরণ ও জামিনের আবেদনে বিরক্ত হয়ে বিচারক নাকি বলেছিলেন, ‘আপনারা বারবার এ কী করেন’? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, ‘আমরা অনেক কিছুই করতে পারি, কিন্তু একটি আদর্শ নিয়ে চলি বলে তেমন কিছু করি না’। এই সময় তিনি নাকি গরাদের একটি লোহার রড হাত দিয়ে বাঁকিয়ে দিয়েছিলেন। বাস্তবে ‘খোদো-ই খিদমতগার’ বাহিনীর পাঠান সৈনিকদের পুলিশের নির্মম অত্যাচার সহ্য করেও অহিংসা নীতির অনুসরণ বিশ্বকে চমকে দিয়েছিল। আসলে গান্ধীজী ক্ষমতা বলে নয়, নৈতিক বলে বলীয়ান হয়ে জাতিকে জয়লাভ করাতে চেয়েছিলেন। গান্ধীজীর নিকট স্বাধীনতা অর্জনের অর্থ কেবলমাত্র বৈদেশিক শাসনের অবসানই ছিল না, সকল প্রকার বৈষম্য, অনাচার ও উৎপীড়নের হাত থেকে অসহায় নিপীড়িত শ্রেণীর মুক্তি অর্জনই ছিল তাঁর কাছে প্রকৃত স্বাধীনতা। ভারতীয় দুই বৃহত্তর জাতি গোষ্ঠী হিন্দু- মুসলমানের ঐক্য প্রতিষ্ঠা ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম প্রধান ব্রত। অস্পৃশ্যতা নিরসন ছিল তাঁর অন্যতম প্রধান সামাজিক কর্মসূচি। নিম্ন বর্ণের সামাজিক উন্নয়ন প্রশ্নে আম্বেদকরের সাথে তাঁর বিতর্কের ক্ষেত্র থাকলেও তথাকথিত নিম্ন বর্ণের মানুষকে পৃথক করে রাখা হিন্দু ধর্মের একটি পাপ হিসেবে মনে করতেন। তাঁর প্রকাশিত’ হরিজন’ পত্রিকায় একাধিকবার হরিজনদের রাজনৈতিক কারণে নয়, সামাজিক ও নৈতিকতার কারণেই হিন্দু’ হিসেবে গণ্য করার পক্ষপাতী ছিলেন। গান্ধীজী যে ভবিষ্যৎ ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন সেখানে প্রতিটি ভারতীয় তার নিজ ধর্ম, ভাবনা, বিশ্বাস, পেশা ও সংস্কৃতিগত স্বতন্ত্রতা বজায় রেখেও বৃহত্তর ভারত জাতির একজন সদস্য হবেন। গান্ধী কল্পিত.ভারত আর বর্তমান ভারত এক নয়। এটা এমন এক ভারত, যে ভারত শাসকের দাবি অনুযায়ী ‘এক’ নয়। গান্ধী অনুসৃত অহিংস পথের পথিক নয়, তার মন আলাদ, তার পথ আলাদা, তার দাবিগুলোও. আলাদা। এই দাবির বক্ষ ভেদ করে নরেন্দ্র মোদী-অমিত শাহের বিচক্ষণতায় তৈরি নয়া ভারত নির্মাণ’ প্রকল্প অহিংসা ও সত্যাগ্রহ নীতির আলোকে আলোকিত নয়, আগ্রাসনের ভাবধারায় পুষ্ট।
‘ইয়ং ইন্ডিয়া’ পত্রিকায় গান্ধীজী ব্রিটিশ শাসনের অনৈতিকতা বিশ্লেষণ করে এবং ভারতীয় জনসমাজের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত ভিন্নতার কথাকে মর্যাদা দিয়ে যে নতুন জাতি কল্পনার কথা ধারাবাহিকভাবে লিখতেন, তার মৌলিক দিকগুলি গণপরিষদের সদস্যগণ সংবিধানে স্থান দিয়েছেন। সংবিধানের প্রস্তাবনায় উল্লেখিত ‘আমরা’ শব্দের উজ্জ্বল উপস্থিতি দিয়ে সুচনা, ভারতীয়দের স্বাধীন, সার্বভৌম, ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্তিক দেশের নাগরিকের মর্যাদ দিয়েছে।’ প্রজা ‘থেকে ‘নাগরিক’ এ উত্তরণের মহাপ্রাপ্তির স্বীকৃতি দান করেছে। পরিতাপের বিষয়, ‘নয়া ভারত’ নির্মাতার আসনে অধিষ্ঠিত রাজনীতির কারবারীরা সংবিধানের মর্যাদাকে উপেক্ষা করার নিরলস প্রয়াস চালিয়ে নিজেদের পরিকল্পিত ছকে যে ভারত নির্মাণ করতে চাইছেন সেটা গান্ধীজীর আদর্শের সাথে বড্ড বেমানান। দিবালোকের মতোই সত্য যে,তারা গান্ধীজীর আদর্শকে কাগজ-পত্রে ঠাঁই দিলেও মগজে ঠাঁই দিতে রাজী নয়। তারা আসলে হিন্দু ধর্মের সনাতন ঐতিহ্যকে অনুধাবন করতে পারেননি, প্রয়োজনও মনে করেননি। আসলে তাঁরা ভারতবর্ষকে চিনতেও পারেননি। তাই, মহাত্মা র মাহাত্ম্যকেও চেতনার জগতে স্থান দেননি। শহীদ দিবসের স্মৃতি তর্পনে এ কথায় বিশেষভাবে স্মরণীয় যে, ভারতীয় জনমানসে অহিংস সত্যাগ্রহ নীতির মাহাত্ম্যের ক্ষয় নেই, কারণ এই নীতি চিরন্তন, শাশ্বত এবং অমিতাভ।